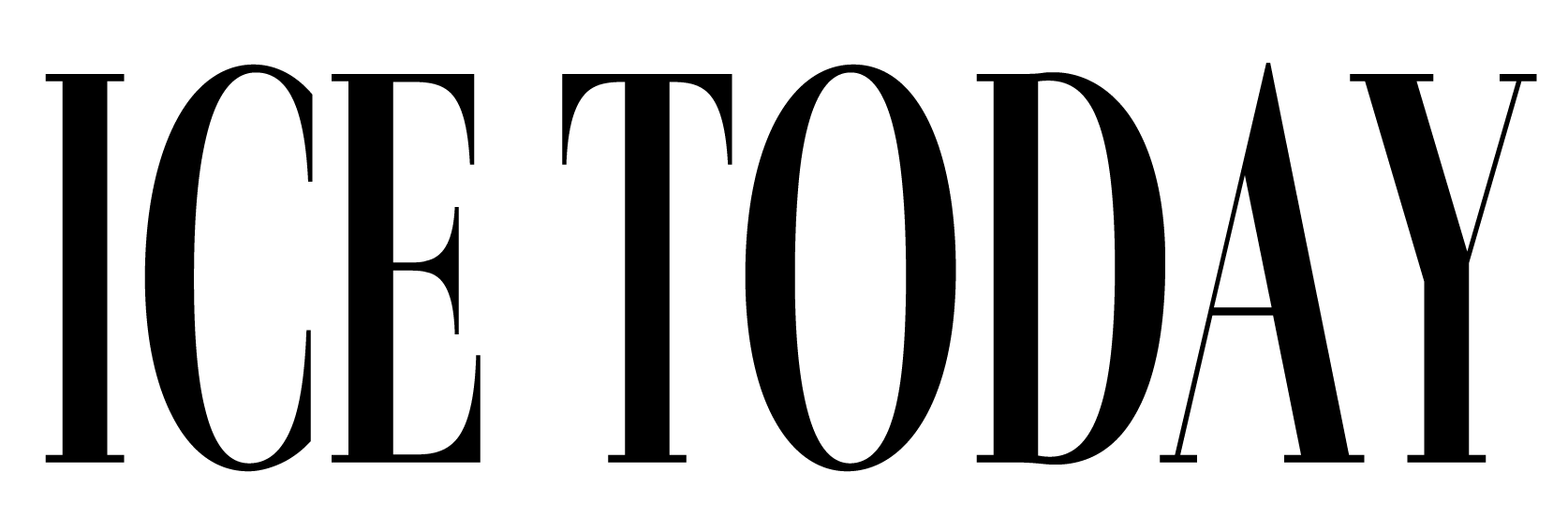বাংলায় দুর্গাপূজার শুরু ঠিক কবে থেকে এ নিয়ে নানান পণ্ডিত-গবেষকের নানান মত থাকার পরেও মোটামুটি একটি বিষয়ে সবাই একমত যে, ষোড়শ শতকে সম্রাট আকবরের শাসনামলে রাজশাহীর তাহিরপুর অঞ্চলের সামন্ত রাজা কংস নারায়ণ ঐতিহাসিকভাবে বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম মহাআড়ম্বরে শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেসময়ের পূজা মোটেও আজকের দিনের মতো ছিলো না। তৎকালীন হিন্দু সমাজ গোত্র-বর্ণ দ্বন্দ্বে তখন এতটাই বিভক্ত যে দুর্গাপূজা তখনো সার্বজনীন হয়ে উঠার সুযোগ পায়নি। উৎসবে অন্য ধর্মের মানুষদের সাদরে বরণ করে নেয়া তো অনেক দূরের ব্যাপার, ব্রাহ্মণ বাড়ির পূজায় বৈশ্য-শুদ্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিলো। তাছাড়া, ধনীসমাজ ছাড়া পূজা আয়োজন করাটাও সবার পক্ষে সম্ভবপর ছিলোনা। তাই সমাজের একটা বিশাল অংশ এই পুরো আয়োজনে ছিলো শুধুই দর্শক।

জমিদারি প্রথাকালীন সময়ে এই পূজার রূপ ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিভিন্ন এলাকার জমিদারেরা দুর্গাপূজাকে নিজ পরিবার ও বংশের সম্মান- আভিজাত্যের বিষয় হিসেবে দেখতেন। তাই এই পূজায় অর্থলগ্নিতে কারো কোনো কমতি থাকতো না। পাশাপাশি অঞ্চলের জমিদারদের মধ্যে এ নিয়ে নিশ্চুপ প্রতিযোগিতাও হতো। প্রতিমা তৈরির জন্য দূরদূরান্ত থেকে বিখ্যাত কারিগর যোগাড় করে আনতেন জমিদারেরা। মন্ডপ তৈরিতেও থাকতো অর্থ-বিত্ত ও সৃজনশীলতার মুনশিয়ানা। তাছাড়া ইংরেজ বাবুদের মণ্ডপের চাকচিক্য দেখিয়ে, প্রতিমায় ভিন্নতা এনে, উৎসবের নানাবিধ খাবারের আয়োজনে তুষ্ট করে, দামি উপহার দিয়ে খুশি করার প্রচেষ্টা তো থাকতোই। জমিদারদের সাথে এই আয়োজনে অঞ্চলের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ীরাও যোগ দিতেন। ফলে তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টায় পূর্ববঙ্গে দুর্গাপূজা এক অন্য ধরনের প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। পরে আস্তে আস্তে তা এই বাংলাতেও শুরু হয়। যদিও পূজা হতো তখন বাড়ি কেন্দ্রিক, বংশ কেন্দ্রিক। এমনকি এখনো দেশের গ্রামীণ এলাকাগুলোতে দেখা যায়, বিভিন্ন এলাকার বড় বড় পূজা গুলো “রায়বাড়ির পূজা”, “মুখুজ্জ্যে বাড়ির পূজা” এভাবে বিভিন্ন বংশের নামে পরিচিত। মোদ্দাকথা, দুর্গাপূজা জনপ্রিয় আর সার্বজনীন হয়ে উঠার জন্য উনিশ শতক পর্যন্ত অপেক্ষার দরকার হয়েছিল। বিশেষ করে বললে সেই শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত।

স্বাধীন দেশে আস্তে আস্তে জমিদাররা বিলুপ্ত হতে থাকেন। পূজার ধরন তখন আরেকবার পাল্টায়। দুর্গাপূজা ব্যবসায়ী ও জমিদারদের আলিশান মহল থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। জনাকয়েকের ধর্মীয় আচার থেকে পরিণত হয় সমাজের সকল শ্রেণির উন্মুক্ত উৎসবে। খেটে খাওয়া শ্রমিক-মজুর-কৃষকরাও তাদের বাৎসরিক আনন্দ উৎসব হিসেবে দুর্গাপূজাকে বরণ করে নেয়। অন্য ধর্মের মানুষেরাও উৎসবের আনন্দে গা ভাসাতে কার্পণ্য করেনি।
এরপর দুর্গাপূজায় দিন দিন সাম্য, সৌহার্দ্য ও অংশগ্রহণ শুধু বেড়েছেই। শহুরে পূজা হয়েছে বিভিন্ন মন্দির আর হাউজিং সোসাইটিভিত্তিক। বিভিন্ন এলাকার সনাতন ধর্মাবলম্বীরা একত্র হয়ে চাঁদা তুলে আয়োজন করছেন পূজা। সেই পূজায় বিভিন্ন বয়সের মানুষের আগমন নিশ্চিত করতে নানান ইভেন্ট রাখা হচ্ছে। পূজা মণ্ডপের চারপাশে উৎসবের আমেজ রাখতে বসেছে মেলা, স্টলে স্টলে থাকছে পূজার নাড়ু-লাড্ডু আর ছানা থেকে শুরু করে রকমারি সব খাবারের আয়োজন, শিশুদের আনন্দের কথা ভেবে রাখা হয়েছে চরকি-নাগরদোলাও। এসবই করা হয়েছে আয়োজনটিকে সকলের জন্য একটি উৎসবে পরিণত করতে। সেই আয়োজনে অন্য ধর্মের মানুষদের অংশগ্রহণও এখন আর শুধুই দর্শক হিসেবে সীমাবদ্ধ নেই, আয়োজক হিসেবেও তারা সাহায্য করছে। মন্দিরগুলোও দুর্গাপূজাকে শুধু আর ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না করে, তাকে সকল মানুষের উৎসবে পরিণত করেছে। পূজায় এখন আর বর্ণ-গোত্র নিয়ে কোন ভেদাভেদ নেই। মণ্ডপে ঢুকে দেবী দর্শন করতে চাইলে আপনি অন্য ধর্মের বলে বা ব্রাহ্মণ না বলে কেউ আপনাকে আটকাবে না। সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটা বোধহয় এটাই।

তবে সেকালের জমিদারদের মতোই একালের এলাকাবাসীর পূজার মধ্যেও রয়ে গেছে দুর্গা বরণে অন্যকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। নগরের ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন পূজা মণ্ডপে গেলে নীরব প্রতিযোগিতাটা চোখে পড়বে। মন্দিরগুলোও প্রতিমা নির্মাণে, মণ্ডপ সজ্জায় প্রতিবার নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে আসার চেষ্টা করছে যেন বাকিদের ছাপিয়ে যাওয়া যায়। তবে আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে, প্রতিযোগিতাটি অসুস্থ না। এর ফলে অবশ্য রেষারেষি হচ্ছে না, বরং প্রতিবছর এই উৎসব উদযাপনের শিল্পমান বাড়ছে।
হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অনুসারে, দেবী দূুর্গা ‘দুর্গতিনাশিনী’ বা সকল দুঃখ-দুর্দশার বিনাশকারিনী। ‘সকল আসুরিক শক্তির দমন হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্য’- দুর্গাপূজার মূল বাণী এটিই। অতীতের জমিদারবাড়ির অন্দরমহল থেকে এই যে দেবী দুর্গা আজ পুরান ঢাকার অলিতে গলিতে বর্ণ-গোত্র-ধর্ম ভেদে মানুষের উৎসবের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন, সেটা সেই সাম্যকেই বারবার প্রতিষ্ঠিত করে।